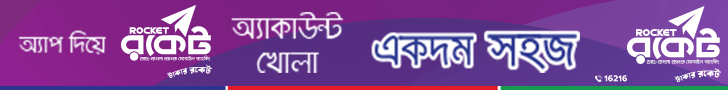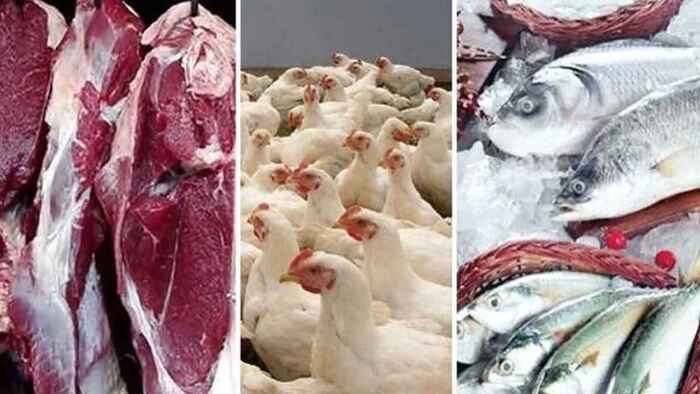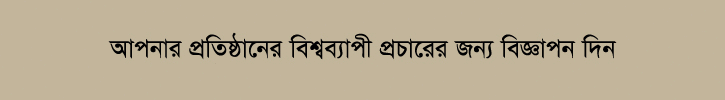- আপডেট টাইম : সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
- ২৪৮ বার পঠিত
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তিস্তার পানি ভাগাভাগি নিয়ে একটি খসড়া চুক্তির রূপরেখা তৈরি হয়ে আছে অন্তত এক যুগ পূর্বে। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং পশ্চিববেঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিরআপত্তির কারণে তিন্তা চুক্তি আজও আলোর মুখ দেখেনি। তবে তিস্তা ইস্যু নিয়ে ভারত নতুন করে আলোচনায় বসতে চায় বাংলাদেশের সাথে। এই আলোচনায় কি প্রস্তাব দেবে ভারত? আর পশ্চিম বঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জির অবস্থানই বা কি হবে?
এমন শঙ্কাকে সামনে রেখেই জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী শুক্রবার দিল্লী যাচ্ছেন। এই সফরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে তিস্তা নদীর পানি চুক্তি নিয়ে আলেচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
কূটনৈতিক সূক্রগুলো বলছে, তিস্তার পানি ভাগাভাগি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করেন না তারা। এ নিয়ে খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের একজন নেতাকে উদ্ধৃত করে ভারতের একটি মিডিয়ায় বলা হয়েছে, মমতা ব্যানার্জি তিস্তা চুক্তির বিরুদ্ধে নন এটি যেমন সত্য, তেমনি ‘পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে’ কোনও চুক্তি করার চেষ্টা হলে তিনি (মমতা ব্যনার্জি ) সেটা কিছুতেই মেনেও নেবে না।
মমতা ব্যনার্জির কারণে ২০১১ সালে তিস্তা চুক্তি যে জায়গায় আঁটকে গিয়েছিল, আজও তৃণমূল কংগ্রেসের সেই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে-এমনটি মনে করেন না নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের সাবেক এক কর্মকর্তা। তার মতে, ওই সময়টাতে তিস্তা চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছিল নদীর প্রবাহ বজায় রাখার জন্য একটা নির্দিষ্ট অংশ ছেড়ে দিয়ে। আর তিস্তার বাকি পানি দুই দেশের মধ্যে সমান ভাগাভাগির কথা বলা হয়েছিল। যদিও উভয় দেশের কেউই এই চুক্তির খসড়াটি প্রকাশ করেনি।

বাংলাদেশে সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের- ফাইল ছবি।
কিন্তু এখন মমতা ব্যানার্জির দাবি শুষ্ক মৌসুমে ভারতের হিস্যা বাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের তিস্তা অববাহিকার জেলাগুলোকে বাড়তি সেচের পানি পাইয়ে দেওয়া।
বাংলাদেশের পক্ষে মমতা ব্যানার্জির এমন অসম প্রস্তাব মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। ভারত যদি অর্ধেকের চেয়ে বেশি পানি পায় এবং বাংলাদেশের হিস্যা ৫০ শতাংশর নিচে নেমে যায়, সেটা বাংলাদেশের জন্য ‘রাজনৈতিক পরাজয়ের’ সামিল হবে।
মমতা ব্যনার্জি মুখে বাংলাদেশের জন্য যতটা আন্তরিক, অন্তরে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে এক চুল ছাড় দিতেও সম্মত নন। তার এই মানসিকতা থেকেই ২০১৭ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় দিল্লীতে মমতা ব্যানার্জি নিজেই তিস্তার পানি ভাগাভাগি নিয়ে বিকল্প একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ওই প্রস্তাবনায় তিনি বলেছিলেন, তিস্তার পানি না-দিতে পারলেও উত্তরবঙ্গে তোর্সা-দুধকুমার-সঙ্কোশ-ধরলার মতো আরও যে সব নদীতে উদ্বৃত্ত পানি আছে তা খাল কেটে বাংলাদেশের তিস্তা অববাহিকায় পাঠানো যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।
বাংলাদেশ এটি জানে এবং এই প্রস্তাবনা মেনে নেওয়ার অর্থই হচ্ছে তিস্তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হওয়া। সেইসাথে মমতা ব্যনার্জির এমন প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপট তৈরি করা মানেই তিস্তা চুক্তিকে আরও যোজন যোজন দূরে ঠেলে দেওয়া। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের একটি সূত্র জানায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের এই বিকল্প প্রস্তাব থেকে এখনও সরে আসেনি।
এমন পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই শেখ হাসিনার ভারত সফরে দু’দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগি নিয়ে নতুন করে আলোচনার দ্বার উন্মোচন হতে যাচ্ছে। ভারত তিস্তার পানি ভাগাভাগি নিয়ে নতুন করে প্রস্তাব রাখতে যাচ্ছে বাংলাদেশের কাছে। এমন কি থাকছে ওই প্রস্তাবনায়? এ নিয়েও বাংলাদেশের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ-উৎকন্ঠা রয়েছে।
শঙ্কা দেখা দিয়েছে- ভারত পূর্বের চুক্তির প্রস্তাবিত ধারায় পরিবর্তন এনে বা বিকল্প কোনও প্রস্তাব পেশ করে তিস্তা নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু করতে চাইছে কি না? যদিও গত ২৫শে জুলাই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে তাদের রিপোর্ট পেশ করে বলেছে, তিস্তা চুক্তি নিষ্পত্তি করতে বাংলাদেশের সঙ্গে ‘অর্থবহ সংলাপের সূচনা’ করতে চায় তারা। তিস্তার অমীমাংসিত ইস্যু দ্রুত নিষ্পত্তির ডাক দেওয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগতও জানিয়েছে বাংলাদেশ।
এ ব্যপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, তিস্তা নিয়ে দু’দেশের সমঝোতা কিন্তু অনেক আগে থেকেই হয়ে আছে। শুধুমাত্র ভারতের ভেতরে তাদের নিজস্ব সমস্যার জন্য তিস্তা চুক্তি এখনও সই করা যায়নি। এখন তিস্তার পানি ভাগাভাগি নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু করা বা নতুন করে কনসেন্সাস তৈরির কথা বলে তারা আসলে কী বোঝাতে চাইছেন সেটা আমরাও ভাল করে বুঝতে চাইছি। তবে তিস্তার পানি ভাগাভাগির ক্ষেত্রে আলোচনার টেবিলে বাংলাদেশ কোন ছাড় দেবে না।

এক ফ্রেমে শেখ হাসিনা ও মমতা ব্যনার্জি- ফাইল ছবি।
ওই কর্মকর্তার মতে, তিস্তা নিয়ে একটি চুক্তিতে উপনিত হতে চায় ভারতের শাসক দল বিজেপিও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও তার দল তৃণমূলের বাধাতেই তা সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যপারে দিল্লীর বক্তব্য হচ্ছে-তিস্তা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে, তাই ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ওই রাজ্যের সম্মতি ছাড়া তিস্তা নিয়ে কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি করা সম্ভব নয়। চুক্তি সম্পাদন না করতে পারার যুক্তি হিসেবে ভারত বরাবরই বাংলাদেশকে এ কথা বলে এসেছে।
২০১৯ সালের আগস্টে বাংলাদেশ সফরে এসে ভারতের পররাষ্টমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছিলেন, তিস্তা চুক্তি নিয়ে ভারত সরকারের ‘কমিটমেন্ট’ অপরিবর্তিত আছে।
এমন পরিস্থিতিতে তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগি নিয়ে যে কোন বিতর্কিত প্রস্তাব ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের রাজনীতিতেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কারণ ২০২৪ এর জানুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন আর একই বছর অনুষ্ঠিত হবে ভারতের লোকসভা নির্বাচন।
এ ব্যপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, পুরনো চুক্তির খসড়াটি অবিকৃত রেখেই নতুন করে আলোচনার কথা বলা হচ্ছে, নাকি ভারতের পার্লামেন্টারি কমিটি সম্পূর্ণ নতুন আকারে চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসতে চাইছে-আমরা আলোচনার টেবিলে বসলেই তা জানতে পারবো।
ভারত-ভিত্তিক গ্লোবাল থিংক-ট্যাংক
এদিকে ভারত-ভিত্তিক গ্লোবাল থিংক-ট্যাংক মনে করেন, তিস্তা নদীর পানি সমবণ্টন হলে একটি যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা অববাহিকা অঞ্চলে পানির প্রবাহ বাড়িয়ে উভয়দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব।
সমস্যা হলো, দুটি দেশই নিজেদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিতর্কিত আন্তঃসীমান্ত নদীপ্রবাহ ইস্যুটি বিচার করছে। স্ট্র্যাটিজিক ফোরসাইট গ্রুপ নামে একটি সংস্থা মনে করে, তিস্তা চুক্তি কার্যকর হলে বর্ষার সময় পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে তা কাজে লাগানো যায়৷ শুষ্ক মৌসুমে ফসল চাষের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশী জেলাগুলিতে আর্থিক রূপান্তর আনা যেতে পারে৷ ভারত-বাংলাদেশের নদী কমিশনের এক্ষেত্রে আরো সক্রিয় হওয়া জরুরি।
বিশেষজ্ঞ মহলের অন্যান্য সুপারিশ হলো, পানি-কূটনীতি সমাধানের একমাত্র পথ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক একটা কাঠামো। দ্বিপাক্ষিক স্তরে নিষ্পত্তি যদি না হয়, তাহোলে তা বহুপাক্ষিক স্তরে নিয়ে যেতে হবে। নিতে হবে এক সুসংহত নদী অববাহিকা নির্দেশিকা। উজানের দিকে ভারতের ভৌগলিক অবস্থানের জন্য বেশি দায়িত্ব নিতে হবে ভারতকে।
তিস্তার গুরুত্ব ও উৎপত্তি
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমালয় পর্বতমালার গড় তাপমাত্রা বাড়ছে৷ বর্ষা আসছে দেরিতে৷ ধানচাষের ক্ষতি হচ্ছে। নদীর অববাহিকা ক্রমশ যাচ্ছে শুকিয়ে৷ নীচে নেমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর।

তিস্তার ওপর নির্মীয়মান ভারতের একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বাঁধ-ছবি সংগৃহিত।
হিমালয়ের সাড়ে সাত হাজার ফুট উচুঁতে অবস্থিত হিমবাহ থেকে উৎসারিত ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ তিস্তা নদী সিকিম হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েবাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রবাহপথে তিস্তার সঙ্গে মিশেছে অনেক শাখানদী৷ পশ্চিমবঙ্গ-সিকিম সীমান্তে মিশেছে রংপো নদী। কালিম্পং-দার্জিলিঙ সীমায় রংগিত নদী।
শিলিগুড়ির উত্তরে সেবকে তিস্তা গিয়ে পড়ে সমতলে। নদীর দু’পাশে পাহাড়ি ঢালে ঘন সবুজ বনরাজি। নদীপক্ষে রুপালি বালি। অতীতে তিস্তা নদীর তিনটি ধারা ছিল। করতোয়া, আত্রেয়ী ও পুনর্ভবা। এই তিন ধারার মিলিত নাম ত্রিস্রোতা৷ তারই অপভ্রংশ থেকে নাম হয় তিস্তা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত তিস্তার ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে ভূমিধস ও ভূমিকম্পের আশঙ্কা বেড়ে গেছে। বিঘ্নিত হয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য৷ তার নেতিবাচক প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাংলাদেশ।
পররাষ্ট্র সচিবের ব্রিফিং
এদিকে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ‘জাতিসংঘ পানি সম্মেলন-২০২৩’ নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে তিস্তার পানি ভাগাভাগি বিষয়টি আলোচনা হবে।
পররাষ্ট্র সচিব বলেন, উচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে তিস্তা নদীর হিস্যা নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করে এসেছি। আশা করছি, এবারও প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি তুলবেন। এছাড়া আমাদের তো অন্যান্য ইস্যুও রয়েছে।
মাসুদ বিন মোমেন বলেন, আমাদের ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। ভারতের গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি আছে, আলোচনায় সেটিও তোলা হবে। সব বিষয়ে আমাদের যৌথ নদী কমিশন এবং অন্যরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।
চলতি বছরের মার্চে তিস্তার পানি প্রত্যাহারে পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে দুটি খাল খননের বিষয়ে কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে নয়াদিল্লীর কাছে জানতে চেয়েছে ঢাকা। এরপর প্রায় পাঁচ মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। এ বিষয়ে নয়াদিল্লীর কোনো বার্তা পাওয়া গেছে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, এখনো পাইনি।
নদী ন্দর/এসএইচ