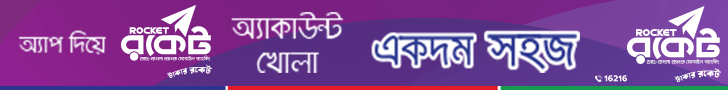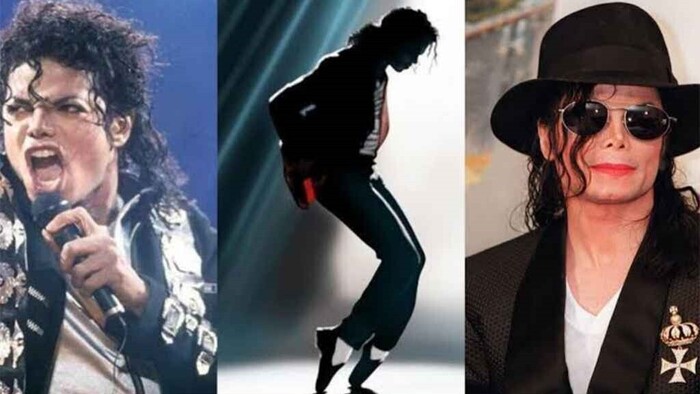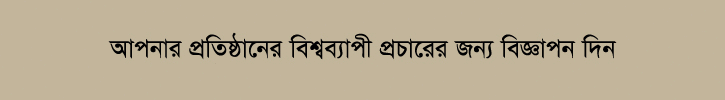- আপডেট টাইম : শনিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
- ৫০ বার পঠিত
৮৩ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন বহু কালজয়ী বাংলা গানের শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাংলা সঙ্গীত দুনিয়া। শিল্পীর প্রয়াণের খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। দুপুর ২টা থেকে বিকেল পৌনে ৫টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য শিল্পীর দেহ রাখা ছিল রবীন্দ্রসদনে। বিকেল সোয়া ৪ টায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হন। তিনি শিল্পীকে মাল্যদান করেন। সমবেদনা জানান প্রয়াত শিল্পীর স্ত্রী সর্বাণী মুখোপাধ্যায়কে। তাকে সব রকম সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিও দেন। রবীন্দ্রসদনে গান স্যালুটের পর তার দেহ ফের তুলে দেওয়া হয় এসএসকেএম হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে। কারণ, প্রয়াত শিল্পী দেহদানের অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন।
প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আধুনিক বাংলা গানের খ্যাতনামী শিল্পী, গীতিকার প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমি শোকাহত। দিন কয়েক আগেই হাসপাতালে গিয়ে শিল্পীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তার মৃত্যুতে বাংলা গানের জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হল। যত দিন বাংলা গান থাকবে তত দিন ‘আমি বাংলায় গান গাই’ বাঙালির মুখে মুখে ফিরবে। আমি গর্বিত, এমন গুণী মানুষকে আমাদের সরকার তার যোগ্য সম্মান জানাতে পেরেছিল। রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান ‘বঙ্গবিভূষণ’ থেকে শুরু করে ‘সঙ্গীত সম্মান’, ‘সঙ্গীত মহাসম্মান’, ‘নজরুল স্মৃতি পুরস্কার’ সবই তিনি পেয়েছেন।’’
তার জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশালে। ১৯৪২ সালে। বাবা প্রভাতচন্দ্র ছিলেন স্কুলশিক্ষক, মা বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় গৃহবধূ। দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়। স্কুলে পড়াকালীনই তার এক আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পান নিকটজনেরা। মাত্র ১২ বছর বয়সে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমি ধান কাটার গান গাই’ কবিতাটিতে সুরারোপ করে বন্ধুদের চমকে দিয়েছিলেন প্রতুল। পাশাপাশি নিজেও লিখতে থাকেন ছড়া, গানের লিরিক। চাকরি করেছেন আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত গেরস্তের মতোই। কিন্তু সেই গেরস্থালির মধ্যেই কোথাও যেন আগুন ছিল। ধিকিধিকি গানের আগুন। বিপ্লব, স্বপ্নভঙ্গ আবার বিপ্লব আর আবার স্বপ্নভঙ্গের বঙ্গীয় রাজনীতির অনেক উথালপাথালের সাক্ষী প্রতুল রাজনৈতিক বিশ্বাসে ছিলেন সমাজতন্ত্রের শরিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোধ হয় মানুষ আর মানবতাকে তার গানে সবার আগে রাখতেন।
কোনও যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়াই শুধুমাত্র ‘বডি পারকাশন’ ব্যবহার করে গানের রেওয়াজ গণনাট্যের গানেও ছিল না। বরং সেখানে গান ছিল যূথবদ্ধ মানুষের হারমনির উপরে দাঁড়িয়ে। ‘কয়্যার’ বা যৌথ গানের সঙ্গে মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াই বা দিনবদলের স্বপ্ন ইত্যাদির অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতুল সে রাস্তায় হাঁটলেন না। তার গান সে অর্থে তাই ‘গণসঙ্গীত’ হয়েও যেন হল না। এমনকি, মঞ্চে গাওয়ার সময়েও (মঞ্চের বাইরেও হাটে-মাঠে-ঘাটে) কোনও যন্ত্রীকে সঙ্গে নিলেন না। কখনও নিজের গাল কখনও বা বুক বাজিয়ে, তুড়ি দিয়ে, হাততালি দিয়ে গাইতে লাগলেন নিজের বাঁধা গান। গায়ক একা হয়েও যেন একা নন। তার সঙ্গী তারই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। প্রতুলের গান গণনাট্যের গানেরই উত্তরাধিকার হলেও তার থেকে তার স্বাতন্ত্র্য প্রধানত ওই এক জায়গাতেই।
গণনাট্যের গানের যৌথতা কি বিপ্লবের স্বপ্নভঙ্গে ছত্রখান হয়ে গিয়েছিল? তার পরে বাংলা মূলধারার গানে সে অর্থে যৌথতা আর দেখা যায়নি। সত্তরের দশকের আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়া গানে (যদিও তার সংখ্যা তেমন বেশি নয়) যৌথতা এক ঝলক উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। ওই পর্যন্তই। বাংলা গানের মূলধারায় তাই ‘কয়্যার’ বা ব্যান্ডের ঐতিহ্য প্রান্তিকই ছিল বলা যায়। নব্বইয়ের দশকে সুমনের উত্থান বাংলা মূলধারার গানের গীতিকার-সুরকার-গায়কের ফর্মুলা তছনছ করে দেয় এবং সুমনের সুবাদেই নব্বইয়ে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে কদম রাখা ছেলেপুলেরা শুনতে শুরু করে ‘এককের গান’।
প্রতুলের প্রথম অ্যালবাম ‘যেতে হবে’ (১৯৯৪) প্রকাশের পর একেবারে অন্য রকম এক শ্রুতির সামনে গিয়ে পড়েন শ্রোতারা। মঞ্চে প্রতুল যন্ত্রানুষঙ্গ বর্জন করলেও এই অ্যালবামে করেননি। তার গানের পিছনে বহু দূরের দিগন্তরেখার মতো থেকেছে যন্ত্র। গানই সেখানে মুখ্য। ইন্টারল্যুডে প্রতুলের নিজেরই কণ্ঠ বেজেছে। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা! সর্বোপরি তার কণ্ঠ, স্বরক্ষেপণ এবং উচ্চারণ। মধুমাখা বাংলা আধুনিকের জগতে সে যেন এক মূর্তিমান ভাঙচুর। ‘সুকণ্ঠ’ নিয়ে গরবে গুমরোনো বাংলা গানের জগতে প্রতুল তার প্রবল রকমের ‘ম্যানারিজম’ নিয়ে যেন সত্তর দশকের কবি সুব্রত সরকারের উচ্চারণেই বলে উঠলেন, ‘সহ্য করো, বাংলাভাষা’।
বাংলা তাকে আদরে-আশ্লেষে বুকে টেনে নিল। ‘বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান, তৃপ্ত শেষ চুমুক’- এমন শব্দচয়ন যে বাংলা গানে উঠে আসতে পারে, তা নব্বই দশকের ফুটতে থাকা কবিকুলও ভাবতে পারেননি। বইমেলার মমাঁর্ত মঞ্চে অথবা না-মঞ্চের জটলাতেও প্রতুল গেয়ে উঠছেন চার্লি চ্যাপলিনের অমর সুরসৃজন ‘লাইমলাইট থিম’-এর বঙ্গান্তর। সেই উচাটন সুরে বসিয়ে দিয়েছেন ভবঘুরে চার্লিকেই উৎসর্গ করা ভালবাসার কথা। চার্লির সুর যদি ব্যক্তিমানুষের একান্ত ভালবাসার অভিজ্ঞান হয়ে থাকে, তবে তাতে প্রতুলের লিরিক ছিল সর্বজনীন ভালবাসার বালুচরি-নকশা। সে গানে যেন লেগে ছিল প্রেমের আবরণ-আভরণহীন উদ্দামতা।
একাধিক সাক্ষাৎকারে প্রতুল বলেছেন, সঙ্গীতের প্রথাগত শিক্ষা তার ছিল না। তার ভাষায়, “আমি শুনে শুনে, ঠেকে ঠেকে শিখেছি।” তার শ্রোতাদেরও প্রথমে হোঁচট খেতে হয়েছিল তার গান শুনতে বসে। একজন মানুষ কণ্ঠ, প্রশিক্ষণ, পরিমার্জন— সব কিছুকে পাশে সরিয়ে রেখে কী করে হয়ে উঠছেন ‘আস্ত একটা গান’, তা আগামী প্রজন্মকে ভেবে উঠতে গেলেও ভাবনার জিমন্যাশিয়ামে ভাবা প্র্যাকটিস করতে হবে। কী করে সম্ভব হয়েছিল তা, এখন আর মনে পড়ে না নব্বই দশকে যুবক হয়ে উঠতে থাকা প্রজন্মের। মাথার উপর এক স্থবির রাজনীতি আর তার সুবাদে চারিপাশে ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’-সুলভ একটা ‘ফিল গুড’ ভাবকে যে হাতেগোনা কয়েক জন দুমড়ে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে প্রতুল অন্যতম।
নদীবন্দর/এএস